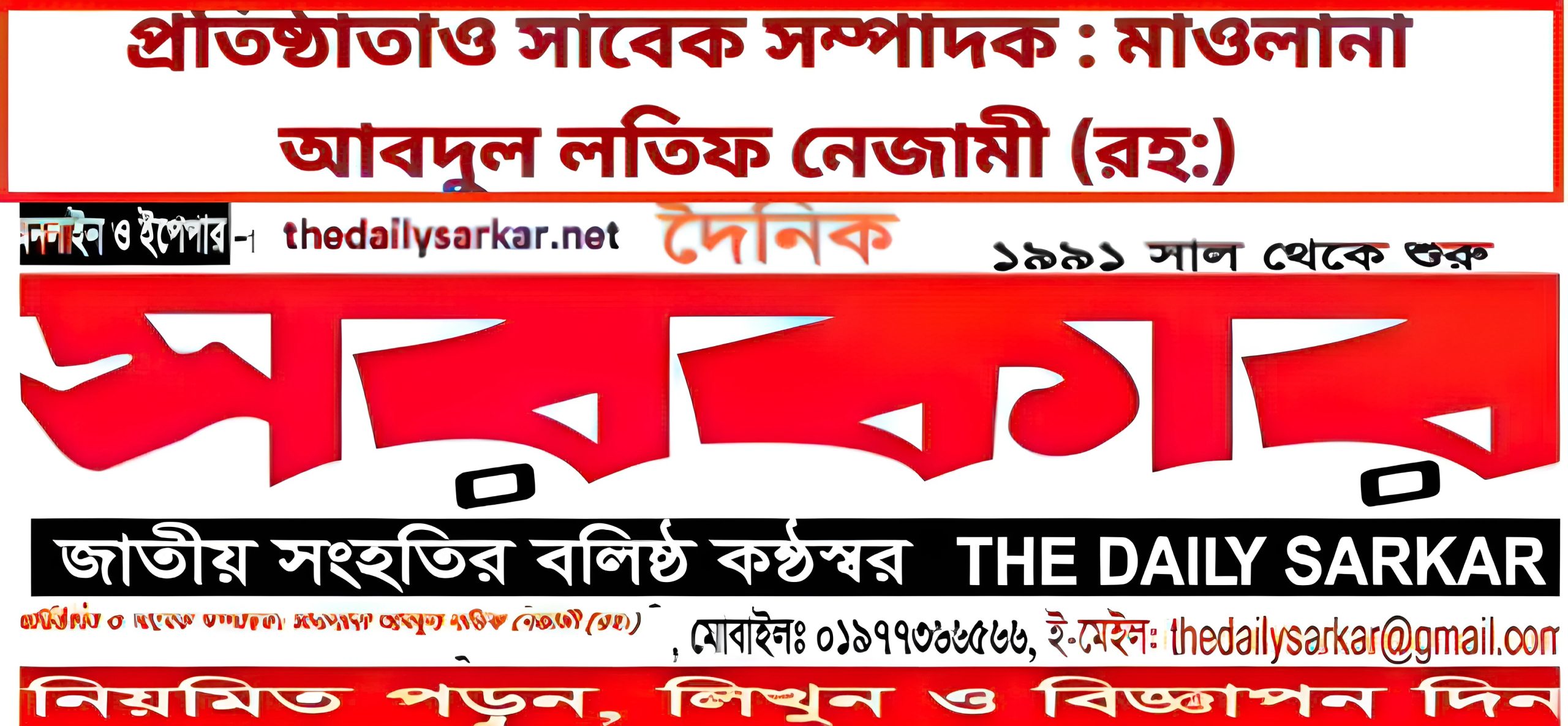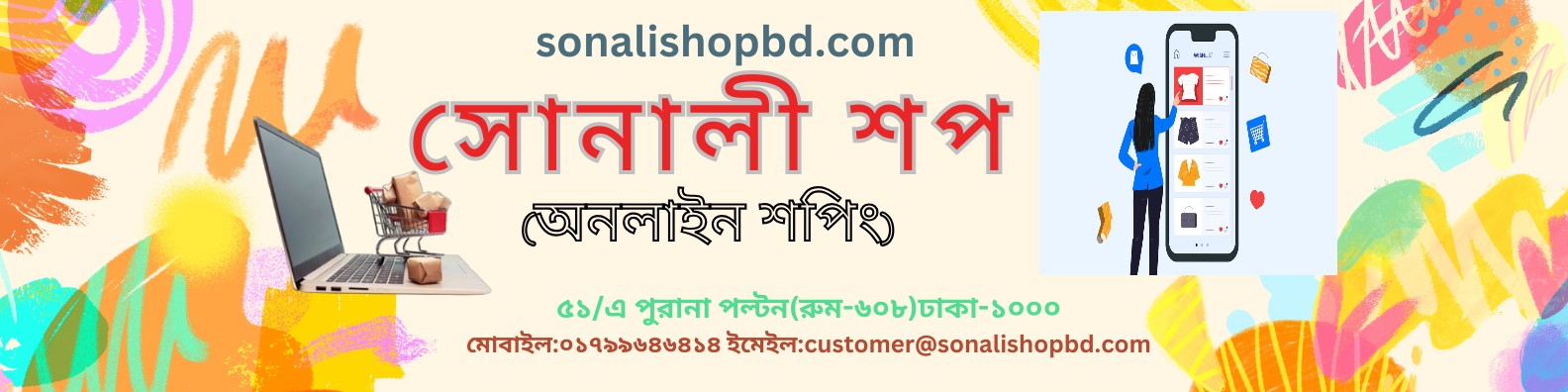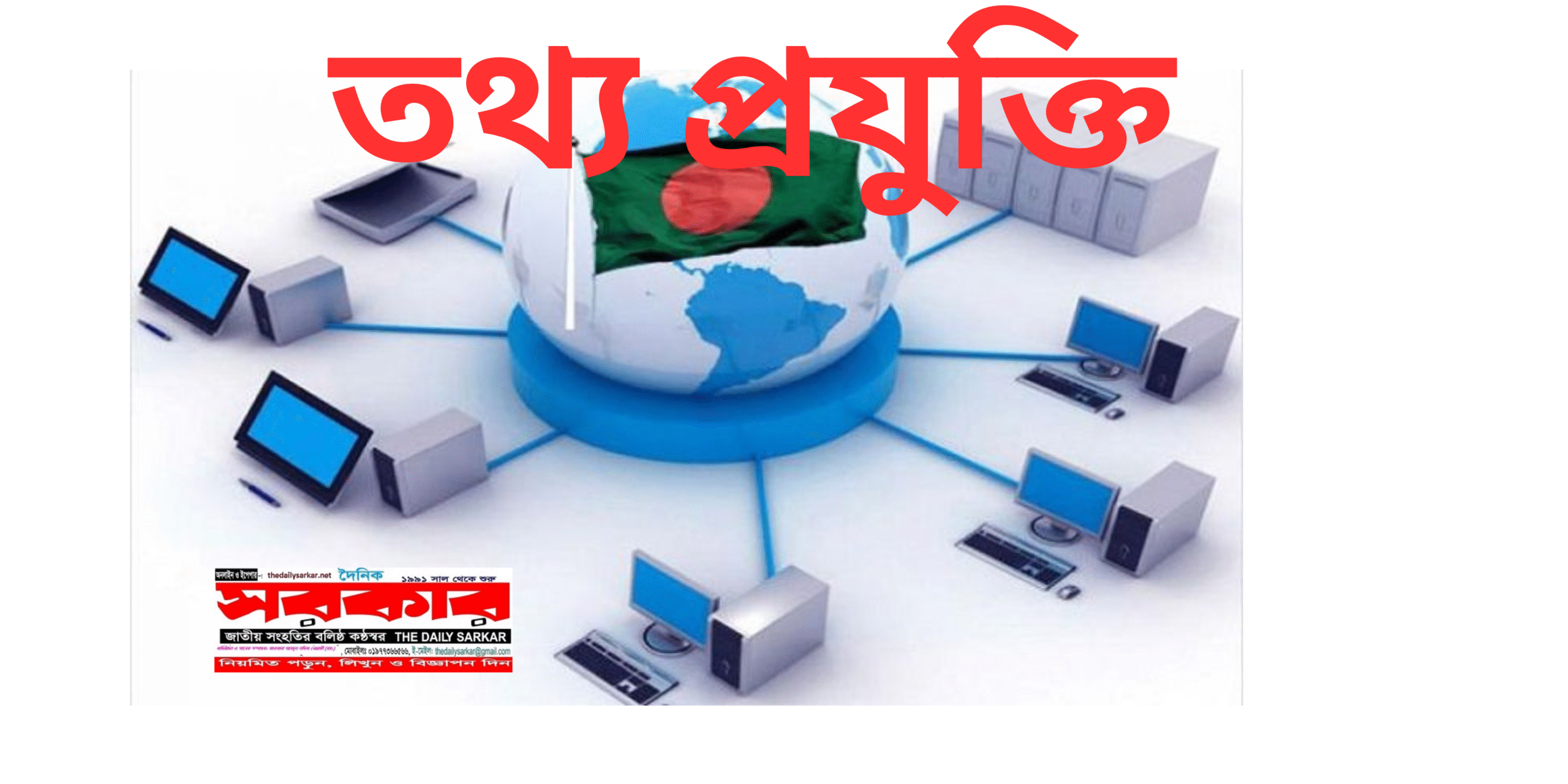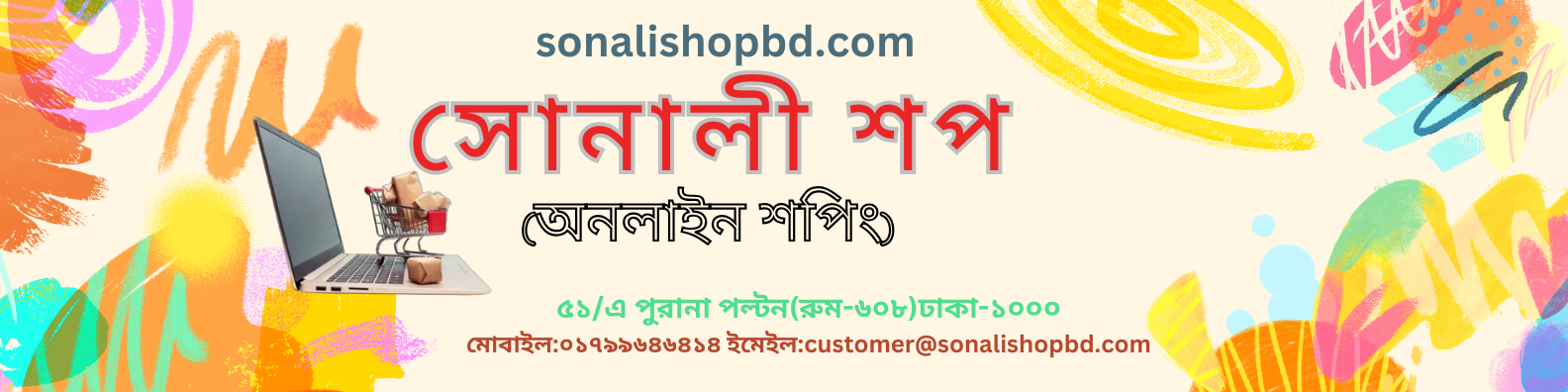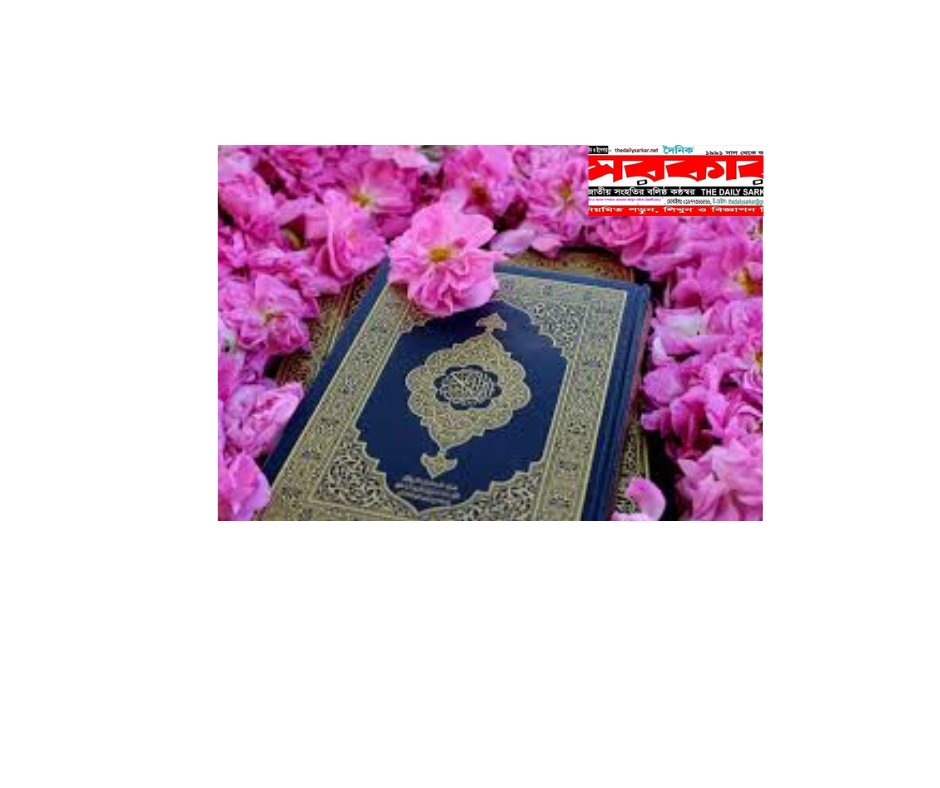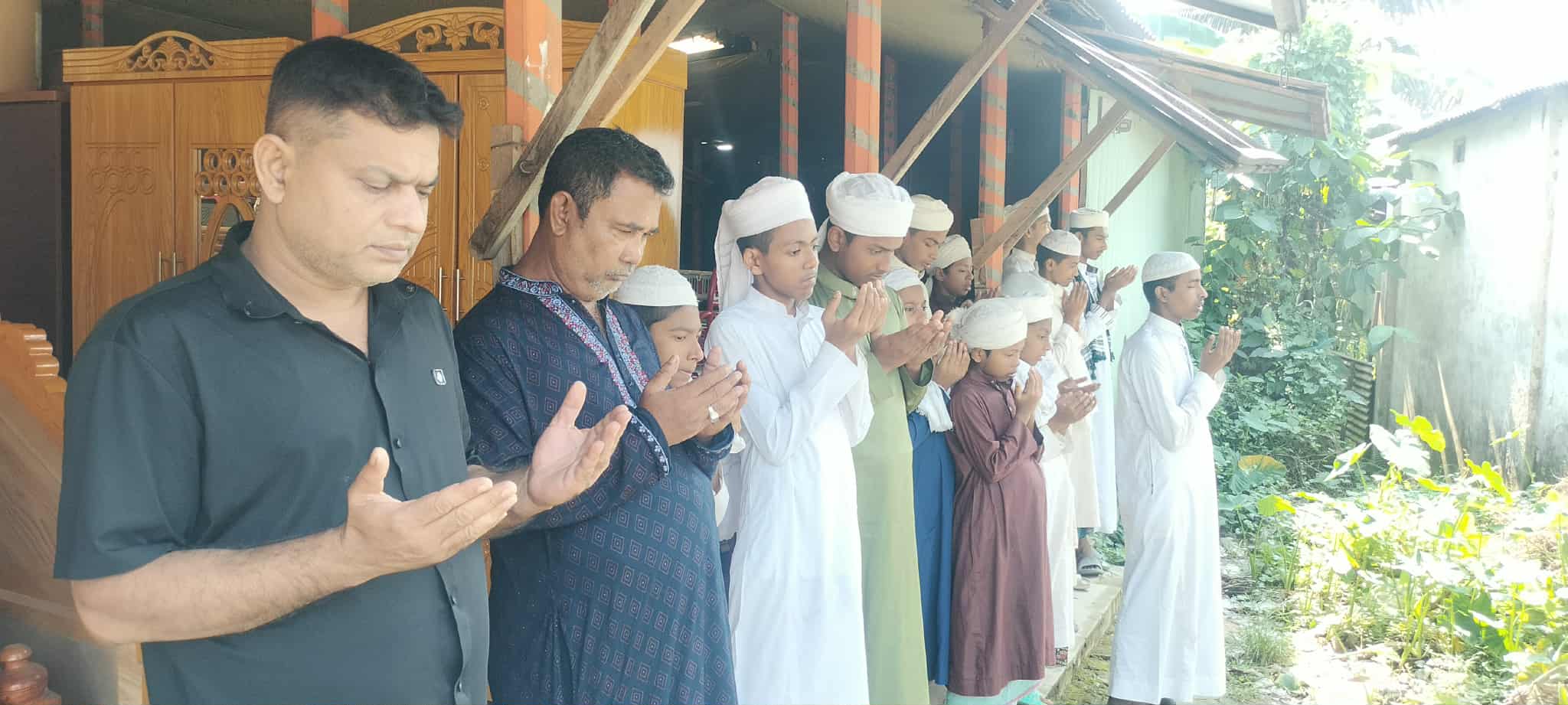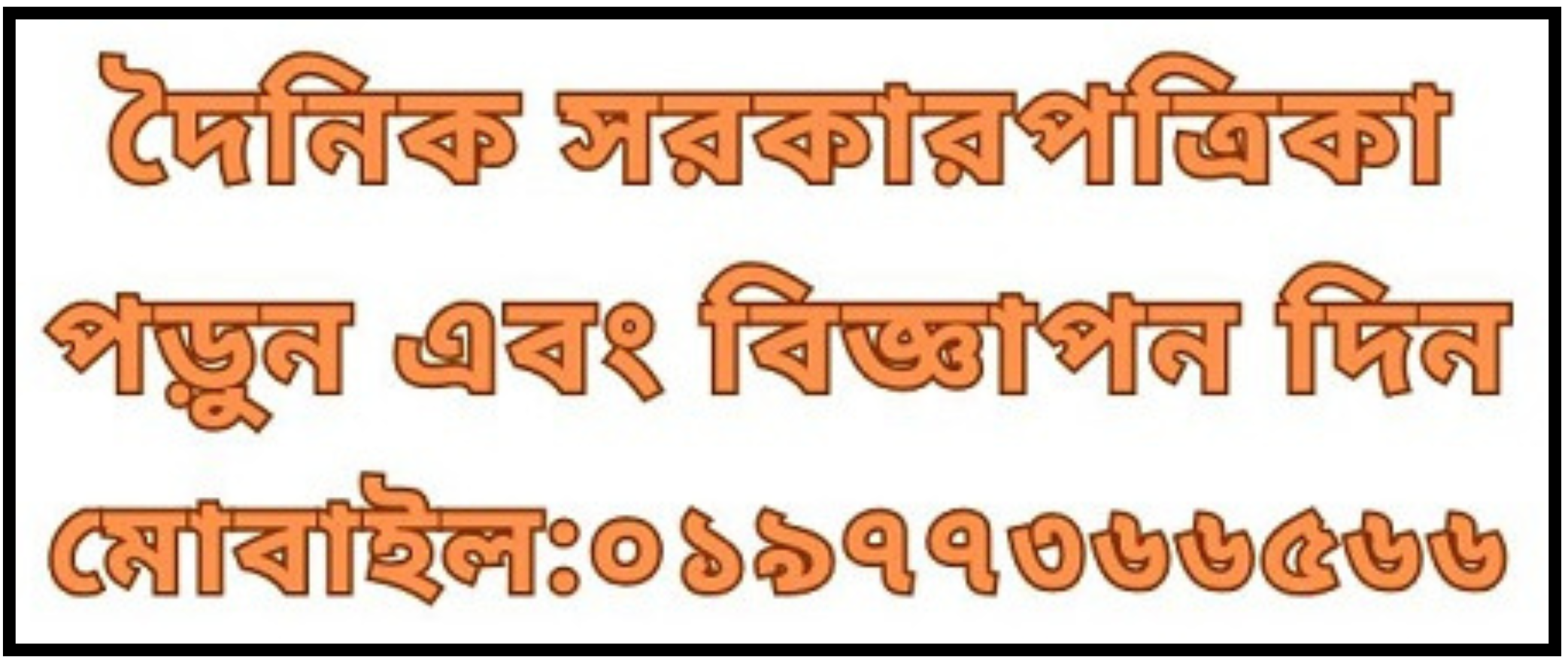যে ১০ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনে বিশ্বকে উন্নতি করে

- Update Time : ০৭:২০:৫১ পূর্বাহ্ন, শনিবার, ১৯ এপ্রিল ২০২৫
- / ৩৪৮ Time View
সরকার ডেস্ক:পরিবর্তন অনিবার্য এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রাণী প্রজাতির বিবর্তনের জন্য জরুরি। কিছু পরির্তন আপনাআপনি হয়। আবার কিছু পরিবর্তন আসে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। ডিএনএ, মাধ্যাকর্ষণ এবং রোগের জীবাণু তত্ত্ব হলো ইতিহাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, যা মানব সভ্যতার গতিপথ চিরতরে বদলে দিয়েছে। বিশ্বকে বদলে দিয়েছে, এমন উল্লেখযোগ্য ১০টি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তথ্য তুলে ধরেছে ডিসকভার ম্যাগাজিন। আবিষ্কারগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।
ডিএন এ
ডিএনএ হলো সেই অণু, যার মধ্যে জীবের জিনগত তথ্য পাওয়া যায়। মা–বাবার বৈশিষ্ট্য সন্তানদের মধ্যে দেখার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান। অনেকেই মনে করেন, ১৯৫০-এর দশকে বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক ডিএনএ আবিষ্কার করেন। তবে সত্যিকার অর্থে ১৮৬৯ সালে সুইজারল্যান্ডের চিকিৎসক ফ্রিদরিশ মিশ্চার এটি প্রথম শনাক্ত করেছিলেন। তিনি একে শনাক্ত করেছিলেন রক্তকণিকায় থাকা ‘নিউক্লিন’ হিসেবে। ওয়াটসন ও ক্রিক ডিএনএ শনাক্ত করার আগপর্যন্ত আরও বেশ কয়েকজন গবেষক এ নিয়ে কাজ করেছেন। সুইজারল্যান্ডের চিকিৎসক ফ্রিদরিশ মিশ্চারের শনাক্ত করা নিউক্লিনই পরবর্তী সময়ে ডিএনএ নাম পায়। ডিএনএ হলো ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের সংক্ষিপ্ত রূপ। জার্মান জৈবরসায়নবিদ আলব্রেখ্ট কোসেলকে এ নামকরণের জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়। কোসেল পরবর্তী সময়ে নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালে দ্বিসূত্রক ডিএনএর গঠন আবিষ্কার করেন জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক। এ আবিষ্কারের জন্য তাঁরা দুজন ১৯৬২ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তবে নোবেল পুরস্কার পেলেও কয়েক বছর পর অভিযোগ ওঠে, রসায়নবিদ রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিনের অনুমতি না নিয়ে তাঁরা তাঁর গবেষণার তথ্য ব্যবহার করেছেন। তাঁর গবেষণার সূত্রেই দ্বিসূত্রক ডিএনএ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিলেন তাঁরা।
পৃথিবীর ঘূর্ণন
পৃথিবী নিজ অক্ষে এবং সূর্যের চারপাশে ঘোরে—এ ধারণা এখন খুবই সাধারণ একটি বিষয়। তবে শুরুর দিকে বিজ্ঞানীদের দেওয়া এ ঘূর্ণন তত্ত্ব অনেকেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তাঁরা বলছিলেন, পৃথিবী ঘুরছে—এটা কীভাবে সম্ভব? পৃথিবী ঘুরলে কি টের পাওয়া যেত না? তবে বিচক্ষণ বিজ্ঞানীদের ক্রমাগত প্রচেষ্টায় পর তা ধীরে ধীরে গ্রহণযোগ্যতা পায়। পৃথিবীর ঘূর্ণন তত্ত্ব আবিষ্কার ও ক্রমান্বয়ে এটিকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীর ভূমিকা আছে। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে বলে প্রথম যাঁরা ধারণা দিয়েছিলেন, তাঁদেরই একজন প্রাচীন গ্রীক জ্যোতির্বিদ আরিসতারকুস। তবে তাঁর সময়ে এ তত্ত্ব ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ, বিশ্বাস করা হতো যে মহাবিশ্বের কেন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও সূর্য—সবাই আমাদের পৃথিবী গ্রহের চারপাশে ঘোরে। গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপার্নিকাসকে মহাবিশ্বের প্রথম সূর্যকেন্দ্রিক মডেল প্রস্তাব করার জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। ১৫৪৩ সালে তিনি তাঁর মহান রচনা ‘অন দ্য রেভল্যুশনস অব দ্য হেভেনলি স্ফিয়ারস’ প্রকাশ করেন। এখানে তাঁর তত্ত্বগুলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি তত্ত্ব ছিল, পৃথিবী তার অক্ষের ওপর ঘূর্ণায়মান হওয়ার মাধ্যমে দিন ও রাত তৈরি হয়। কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মডেলটি পুরোনো টলেমীয় তত্ত্বকে নাকচ করে দেয়। ওই তত্ত্বে দাবি করা হয়েছিল, পৃথিবী স্থির। কোপার্নিকাসের কাজগুলো তাঁর জীবদ্দশায় তেমন একটা পরিচিতি পায়নি। পরে তা গ্রহণযোগ্যতা পায়। গ্যালিলিও গ্যালিলি কোপার্নিকাসের তত্ত্বের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। তিনি একটি টেলিস্কোপ ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছিলেন। ১৬১০ সালে গ্যালিলিও শুক্র গ্রহের পর্যায় এবং বৃহস্পতি গ্রহের চাঁদগুলোকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের পৃথিবীকেন্দ্রিক মডেলের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন তিনি।
গ্যালিলিও এটাও প্রমাণ করেছিলেন, শুক্র গ্রহ যে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করেছে, তা সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করার কারণে হয়েছে। জার্মান গণিতবিদ জোহানেস কেপলার সূর্যের চারপাশে গ্রহগুলোর কক্ষপথের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে একাধিক সূত্র তৈরি করেছিলেন। এই সূত্রগুলো আজও প্রাসঙ্গিক। কোপার্নিকান তত্ত্বের সঙ্গে সংগতি রেখে যথার্থভাবে গ্রহের গতিবিধি নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য এ সূত্রগুলো গাণিতিক সমীকরণ দেয়।
বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাঁর বিখ্যাত ঘুড়ি পরীক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেছিলেন বলে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। অথচ ১৭৫২ সালে চাবি ও ঘুড়ি ব্যবহার করে করা পরীক্ষায় ফ্রাঙ্কলিন প্রমাণ করেছিলেন, বজ্রপাতও বিদ্যুতের একটি রূপ। আরেকটি মিথ হলো, ফ্রাঙ্কলিন বজ্রপাতের শিকার হয়েছিলেন। তিনি আসলে বজ্রপাতের শিকার হননি, ঝড়ের কারণে ঘুড়িটি বিদ্যুতায়িত হয়েছিল। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক থেলিসই প্রথম ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বে পশমকে বাকলযুক্ত গাছের রসের সঙ্গে ঘষার মধ্য দিয়ে স্থির বিদ্যুৎ পর্যবেক্ষণ করেন। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক উইলিয়াম গিলবার্ট প্রথম ‘ইলেক্ট্রিক’ বা ‘বৈদ্যুতিক’ শব্দটির প্রচলন করেন। গিলবার্টকে ‘বিদ্যুতের জনক’ হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। গিলবার্টই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ‘চৌম্বক মেরু’, ‘বৈদ্যুতিক বল’ ও ‘বৈদ্যুতিক আকর্ষণ’—এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছিলেন। ১৬০০ সালে তাঁর ছয় খণ্ডের বইয়ের সেট ‘ডি ম্যাগনেট’ প্রকাশিত হয়েছিল।
রোগের জীবাণু তত্ত্ব
রোগের জীবাণু তত্ত্বটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি বৈজ্ঞানিক নীতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ তত্ত্বে অনেক রোগের কারণ হিসেবে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মতো অণুজীবকে দায়ী করা হয়েছে। তত্ত্বটি রোগের কারণ সম্পর্কে পূর্ববর্তী বিশ্বাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছিল। রোগের জীবাণু তত্ত্বটি দিয়েছিলেন লুই পাস্তুর। তিনি দেখিয়েছিলেন, জীবন্ত অণুজীবগুলো পচন ঘটায়, এতে দুধ ও ওয়াইন টক হয়ে যায়। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, তাপ প্রয়োগ করার মাধ্যমে এসব অণুজীব ধ্বংস করা সম্ভব। এ প্রক্রিয়াকে আমরা এখন পাস্তুরীকরণ হিসেবে চিনি। এ তত্ত্ব গেম চেঞ্জার হিসেবে কাজ করেছিল। পাস্তুরিত না করা খাবারে থাকা ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষের অসুস্থ হওয়া ঠেকাতে এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। লুই পাস্তুর তাঁর তত্ত্ব দেওয়ার আগপর্যন্ত মানুষ বিশ্বাস করত, শরীরের ভেতর থেকে রোগের জন্ম হয়। পাস্তুর তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন, জীবাণু তত্ত্ব সত্য এবং শরীরে অণুজীবের আক্রমণের কারণে রোগ বাসা বাঁধে। পাস্তুরের চেষ্টায় মানুষের মনোভাবে পরিবর্তন এসেছিল এবং জীবাণু তত্ত্ব আরও বেশি করে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল।
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি
গাছ থেকে আপেল পড়ার দৃশ্য দেখে গণিতবিদ ও পদার্থবিদ আইজ্যাক নিউটনের মাথায় একটি ভাবনা এসেছিল। আর সে ভাবনাকে ভিত্তি করে মাত্র ২৩ বছর বয়সে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। নিউটন ভাবছিলেন, কীভাবে কোনো একটি বল বা শক্তি বস্তুগুলোকে সরাসরি মাটিতে টেনে আনে। মাধ্যাকর্ষণই ছিল এর উত্তর। এটি এমন একটি শক্তি, যা বস্তুগুলোকে একে অপরের দিকে টেনে আনে। একটি বস্তুর ভর যত বেশি হয়, বল বা মহাকর্ষীয় টান তত বেশি হয়। যখন বস্তুগুলো বেশি দূরে থাকে, তখন বল তত দুর্বল হয়। নিউটনের কাজ এবং তাঁর মাধ্যাকর্ষণ–সম্পর্কিত তত্ত্বটি বেসবলের গতিপথ থেকে শুরু করে সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর কক্ষপথ পর্যন্ত সবকিছু ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নিউটনের আবিষ্কারগুলো এখানেই থেমে থাকেনি। ১৬৮৭ সালে নিউটন তাঁর ‘প্রিন্সিপিয়া’ বইটি প্রকাশ করেন। মাধ্যাকর্ষণ সূত্র ও গতির তিন সূত্র নিয়ে সেখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাঁর কাজগুলো আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করেছিল।
রোগের জীবাণু তত্ত্ব যেমন আধুনিক চিকিৎসায় বিপ্লব তৈরি করেছে, তেমনি এর হাত ধরে অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার হয়েছে। আর এ আবিষ্কার অগণিত মানুষের জীবন রক্ষায় ভূমিকা রাখছে। মাইক্রোবায়োলজি সোসাইটির তথ্যমতে, মানুষ সহস্রাব্দ ধরে কোনো না কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে আসছিল। তবে নির্দিষ্ট কিছু সংক্রমণের জন্য যে ব্যাকটেরিয়া দায়ী, সেটা বোঝার পর আগে থেকে প্রস্তুত করা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে চিকিৎসা নিতে পারছে। ১৯০৯ সালে জার্মান চিকিৎসক পল এয়ালিশ লক্ষ করেন, কিছু রাসায়নিক রঞ্জক পদার্থ নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়া কোষকে অন্যদের মতো রঞ্জিত করে না। এ কারণে তিনি বিশ্বাস করতেন, আশপাশের অন্য কোষগুলোকে না মেরে নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলা সম্ভব। সিফিলিসের চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কার করেন এয়ালিশ, যেটিকে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের অনেকেই প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক বলে উল্লেখ করে থাকেন। তবে এয়ালিশ তাঁর আবিষ্কারকে কেমোথেরাপি বলে উল্লেখ করেন। কারণ, এ পদ্ধতিতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে রাসায়নিক ব্যবহার করা হতো। এয়ালিশের আবিষ্কারের জন্য তাঁকে ‘ইমিউনোলজির জনক’ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মাইক্রোবায়োলজি সোসাইটির তথ্যমতে, ইউক্রেনীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন অনুজীববিজ্ঞানী সেলম্যান ওয়াক্সম্যান প্রায় ৩০ বছর পর ‘অ্যান্টিবায়োটিক’ শব্দটির প্রচলন করেন।
বর্তমানে পরিচিত সবচেয়ে স্বীকৃত অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর একটি পেনিসিলিন। চিকিৎসকেরা প্রতিবছর লাখ লাখ রোগীকে এই অ্যান্টিবায়োটিক লিখে দেন। তবে সুপরিচিত এই অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার হয়েছে আকস্মিকভাবে। ১৯২৮ সালে স্কটিশ অণুজীববিজ্ঞানী আলেক্সান্ডার ফ্লেমিং কিছুদিন বিরতির পর পরীক্ষাগারে গিয়ে দেখেন, পেনিসিলিয়াম নোটাটাম নামের একটি ছত্রাক একটি কালচার প্লেট থেকে স্ট্যাফ ব্যাকটেরিয়াকে সরিয়ে দিয়েছে। ফ্লেমিং দেখেন, ছত্রাকটি প্লেটে ব্যাকটেরিয়ামুক্ত জায়গা তৈরি করেছে। একাধিক পরীক্ষার পর ফ্লেমিং সফলভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হন, পি. নোটাটাম ছত্রাক স্ট্যাফ ব্যাকটেরিয়ার বিস্তার ঠেকিয়েছে। দ্রুতই পেনিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিকটির ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয়। এটি ব্যবহার করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।
বিগ ব্যাং তত্ত্ব
মহাবিশ্বের সৃষ্টি কীভাবে হলো, তা নিয়ে দেওয়া তত্ত্বগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হলো বিগ ব্যাং। এ তত্ত্ব অনুযায়ী, ১ হাজার ৩৭০ কোটি বছর আগে মহাবিশ্বের সব পদার্থ একটি ছোট বিন্দুতে পুঞ্জীভূত ছিল। একটি বিশাল বিস্ফোরণের পর মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়। বিগ ব্যাংয়ের কথা প্রথম উল্লেখ করেন বেলজিয়ামের মহাবিশ্ব তত্ত্ববিদ ও ক্যাথলিক ধর্মযাজক জর্জেস লেমাইত্রে। প্রাথমিকভাবে ১৯২৭ সালে লেমাইত্রে সাধারণ আপেক্ষিকতা এবং একে ঘিরে তৈরি হওয়া সমীকরণগুলোর সমাধান সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। তবে এটা অনেকটাই অলক্ষিত ছিল। যদিও অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করতেন না, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। তবু একদল মহাজাগতিক বিজ্ঞানী সে ধারণার বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁদের কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। তেমনই একজন এডউইন হাবল। তিনি যখন দেখলেন, আমাদের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছায়াপথগুলো আমাদের কাছাকাছি থাকা ছায়াপথগুলোর তুলনায় দ্রুত সরে যাচ্ছে, তখন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের ধারণাটি আরও যুক্তিসংগত হয়ে উঠল। লেমাইত্রের ১৯২৭ সালের গবেষণাপত্রটি পরে স্বীকৃতি পায়। লেমাইত্রের ১৯৩১ সালের গবেষণাপত্রে ‘বিগ ব্যাং’ শব্দটি উপস্থাপন করা হয়েছিল।
টিকা
বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন একসময় বলেছিলেন, ‘এক আউন্স পরিমাণ সুরক্ষায় এক পাউন্ড পরিমাণ নিরাময়।’ এর মানে হলো, সামান্য পূর্বসতর্কতায় বড় ক্ষতি এড়ানো সম্ভব। শহরগুলোকে দাবানলের ক্ষতি থেকে বাঁচাতে ফ্রাঙ্কলিন এমন উপদেশ দিয়েছিলেন। তবে স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। টিকার আবিষ্কার বেশ কিছু গুরুতর রোগ প্রতিরোধ এবং মানুষকে নিরাপদ রাখতে সাহায্য করেছে। টিকার কারণে মানুষের পোলিওর মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা অনেকটাই কমে গেছে এবং গুটিবসন্ত নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের (সিডিসি) তথ্য অনুসারে, টিকা হলো এক সুরক্ষাপদ্ধতি। এ প্রক্রিয়ায় মানবদেহে অল্প পরিমাণে কোনো রোগের জীবাণু প্রবেশ করানো হয়, যাতে রোগটি আবার প্রবেশের চেষ্টা করলে তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা শরীরে তৈরি হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে, ১৯৭৬ সালে ড. এডওয়ার্ড জেনার প্রথম টিকা তৈরি করেন। গোবসন্তের ক্ষত থেকে সংক্রমিত উপাদান ব্যবহার করে এ টিকা তৈরি করেছিলেন তিনি। গোবসন্ত হলো গুটিবসন্তের মতো রোগ।
জেমস ফিপস নামের আট বছর বয়সী এক আক্রান্ত শিশুর শরীরে ড. এডওয়ার্ড টিকাটি প্রয়োগ করেছিলেন। এতে দেখা যায়, টিকা প্রয়োগের শুরুর দিকে শিশুটি ভালো বোধ না করলেও পরে সে অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠে। কয়েক মাস পর গুটিবসন্তের ক্ষত থেকে সংক্রমিত উপাদান ব্যবহার করে ফিপসের শরীরে পরীক্ষা চালান এডওয়ার্ড। এতে দেখা যায়, ফিপস সংক্রমিত হয়নি। তখন থেকে গুটিবসন্তের টিকা ব্যবহার করে অগণিত মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।
বিবর্তন তত্ত্ব
বিবর্তনবাদ হলো এমন এক তত্ত্ব, যেখানে বলা হয়েছে, প্রাণীদের এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে জেনেটিক স্তরে পরিবর্তন ঘটে এবং তারা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে প্রাণীর রং বা ঠোঁটের পরিবর্তন হতে পারে। এর সাহায্যে তারা শিকারিদের থেকে লুকিয়ে থাকতে পারে বা শিকারকে আরও ভালোভাবে ধরতে পারে। গালাপাগোসে বসবাসকারী প্রাণীদের নিয়ে বিশেষ করে ফিঞ্চ পাখিদের নিয়ে গবেষণা করার পর প্রকৃতিবিদ চার্লস ডারউইন একটি তত্ত্ব দেন। তিনি বলেন, গালাপাগোসের ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে বসবাসকারী পাখিগুলো একই প্রজাতির হলেও তাদের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। ডারউইন উল্লেখ করেছিলেন, প্রতিটি দ্বীপের ফিঞ্চদের ঠোঁট দেখতে আলাদা আলাদা ছিল। এই ঠোঁটগুলোর সাহায্যে ফিঞ্চরা তাদের নির্দিষ্ট দ্বীপে প্রধান খাদ্য উৎস খুঁজে বের করত। কিছু পাখির বাদাম ও বীজ ফাটানোর মতো বড় ঠোঁট ছিল, আবার কারও কারও ঠোঁট ছিল ছোট ও সরু। এর মধ্য দিয়ে তারা পোকামাকড় খুঁজে বের করত। এই পর্যবেক্ষণগুলোর মধ্য দিয়ে বিবর্তনের জনক উপাধি পেয়েছিলেন চার্লস ডারউইন।১৮৫৯ সালে ডারউইনের ‘অন দ্য অরিজিন অব স্পেসিজ’ প্রকাশের পর বিবর্তন তত্ত্ব পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি আধুনিক বিজ্ঞানীদের কাজের রূপরেখা তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন।
সিআরআইএসপিআর প্রযুক্তি
ন্যাশনাল হিউম্যান জিনোম রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুসারে, সিআরআইএসপিআরের মানে হলো ক্লাস্টার্ড রেগুলারলি ইন্টারস্পেসড শর্ট প্যালিনড্রোমিক রিপিটস। জীবন্ত প্রাণীর ডিএনএ সম্পাদনার জন্য গবেষকেরা এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকেন। সিআরআইএসপিআর আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কয়েকজন মানুষের অবদান আছে। কয়েক দশকের গবেষণার পর এ প্রযুক্তি আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। গবেষকদের মধ্যে আছেন ইয়োশিজুমি ইশিনো, ফ্রান্সিসকো মোজিকা, জেনিফার ডাউডনা এবং ইমানুয়েল শারপঁসিয়ে। সিআরআইএসপিআর আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অবদান রাখায় ডাউডনা ও শারপঁসিয়ে ২০২০ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। গবেষকেরা সিআরআইএসপিআর প্রযুক্তিকে আণবিক কাঁচি হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা ডিএনএকে আলাদা করার পর জিন সম্পাদনা করে। ২০১৮ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, বিজ্ঞানীরা ক্যানসারের মতো রোগ বা বংশগত রোগের কারণ হতে পারে, এমন কিছু জিন এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিস্থাপন করতে পারেন।